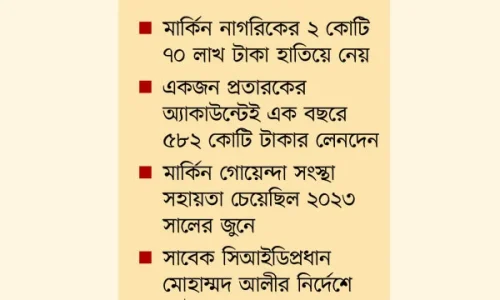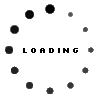সমকাল ২৪ অক্টোবর ২০২৫ , ৪:২২:৫৬
মো. আসাদুজ্জামান
ঢাকার একজন মধ্যবিত্ত নারী মিসেস রহমান (ছদ্মনাম) সম্প্রতি তাঁর স্বামীকে হারিয়েছেন। শোক সামলে ওঠার আগেই তিনি একটি নির্মম বাস্তবতার মুখোমুখি হন। স্বামীর রেখে যাওয়া একমাত্র বড় অঙ্কের সঞ্চয়, যা ব্যাংকে ফিক্সড ডিপোজিট হিসেবে রাখা ছিল, তাঁর নমিনি হিসেবে স্বামীর ছোট ভাইয়ের নাম দেওয়া। মিসেস রহমান এবং তাঁর দুই সন্তান যারা শরিয়াহ আইন অনুযায়ী স্বামীর সম্পত্তির প্রধান উত্তরাধিকারী, এখন এক অনিশ্চিত ভবিষ্যতের সামনে দাঁড়িয়ে। নমিনি হিসেবে দেবর বলছেন, আইন অনুযায়ী এই টাকার মালিক তিনিই। অন্যদিকে উত্তরাধিকার আইন বলছে, এই সম্পদের হকদার মিসেস রহমান ও তাঁর সন্তানরা।
এটি কোনো বিচ্ছিন্ন ঘটনা নয়। এতে দেশের হাজারো পরিবার নীরব সংকট মোকাবেলা করছে, যা মৌলিক আইনি প্রশ্নেরও জন্ম দিয়েছে। যখন কোনো ব্যক্তি মারা যান, তখন তার ব্যাংকে গচ্ছিত টাকার প্রকৃত মালিক কে হবেন– ব্যাংকের ফরমে উল্লিখিত ‘নমিনি’, নাকি ব্যক্তির নিজ ধর্ম ও পার্সোনাল ল অনুযায়ী নির্ধারিত ‘উত্তরাধিকারী’? এই প্রশ্নটি বাংলাদেশের আইনি কাঠামোতে এক গভীর দ্বন্দ্ব ও বিভ্রান্তির সৃষ্টি করেছে, যার সুদূরপ্রসারী সামাজিক ও অর্থনৈতিক প্রভাব রয়েছে। এই বিতর্কের কেন্দ্রবিন্দুতে রয়েছে দুটি ভিন্ন দর্শন ও উদ্দেশ্যের ওপর ভিত্তি করে তৈরি হওয়া আইন। একদিকে রয়েছে ব্যাংক কোম্পানি আইন ১৯৯১-এর মতো বিশেষায়িত আর্থিক আইন, যা আর্থিক লেনদেনের সুবিধার্থে প্রণীত। এই আইনের ১০৩ ধারায় অত্যন্ত স্পষ্টভাবে বলা হয়েছে, আমানতকারীর মৃত্যুর পর মনোনীত ব্যক্তি বা নমিনি ওই আমানতের ওপর আমানতকারীর যাবতীয় অধিকার লাভ করবেন এবং অন্য কোনো ব্যক্তি ওই অধিকার থেকে বঞ্চিত হবেন। এই বিধানের উদ্দেশ্য হলো, আমানতকারীর মৃত্যুর পর ব্যাংক যেন কোনো আইনি জটিলতা ছাড়াই দ্রুত ও সহজে আমানতের টাকা হস্তান্তর করে দায়মুক্তি পেতে পারে। আইনটির কঠোর ভাষা এবং ‘আপাতত বলবৎ অন্য কোনো আইনে যাহা কিছুই থাকুক না কেন’ এই আইনের বিধানই প্রাধান্য পাবে– এই ধরনের ধারার সরল ব্যাখ্যা দাঁড়ায়, নমিনিই আমানতের একচ্ছত্র মালিক।
অন্যদিকে রয়েছে দেশের মানুষের জন্য প্রযোজ্য মুসলিম উত্তরাধিকার (ফারায়েজ) আইন এবং হিন্দু উত্তরাধিকার (দায়ভাগ) আইনের মতো ব্যক্তিগত আইন। ইসলামী আইন অনুযায়ী, কোনো মুসলিম ব্যক্তির মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে তার রেখে যাওয়া সমস্ত সম্পত্তি, যার মধ্যে ব্যাংকে গচ্ছিত অর্থও অন্তর্ভুক্ত, তার উত্তরাধিকারীদের ওপর বর্তায়। কোরআন, সুন্নাহ ও ইজমার ভিত্তিতে নির্ধারিত এই বণ্টন ব্যবস্থা একটি ঐশ্বরিক বিধান হিসেবে বিবেচিত হয় এবং কোনো ব্যক্তির একক ইচ্ছায় যেমন– শুধু একজনকে নমিনি করার মাধ্যমে এই বিধানকে লঙ্ঘন করার সুযোগ নেই। একইভাবে হিন্দু দায়ভাগ আইন অনুযায়ী, যে ব্যক্তি মৃতকে ‘পিণ্ড’ দান করার অধিকারী, তিনিই ‘সপিণ্ড’ হিসেবে সম্পত্তির উত্তরাধিকারী হন এবং এই আইনেরও একটি অলঙ্ঘনীয় ধর্মীয় ও আইনি ভিত্তি রয়েছে।
এ দুই ভিন্নধর্মী আইনের কাঠামো থেকে একটি মৌলিক দ্বন্দ্ব স্পষ্ট হয়ে ওঠে। ব্যাংক কোম্পানি আইন যেখানে লেনদেনের সরলীকরণকে গুরুত্ব দেয়, সেখানে উত্তরাধিকার আইন পারিবারিক ও সামাজিক ন্যায়বিচারকে প্রাধান্য দেয়। এ দুই ভিন্ন দর্শনের সংঘর্ষই নমিনি বনাম উত্তরাধিকারীর বিতর্কের মূল কারণ। আইনের এই সুস্পষ্ট দ্বন্দ্ব নিরসনে ২০১৬ সালে হাইকোর্ট বিভাগ এক যুগান্তকারী রায় প্রদান করেন। বিচারপতি নাঈমা হায়দার এবং বিচারপতি খিজির আহমেদ চৌধুরীর সমন্বয়ে গঠিত বেঞ্চ এক ঐতিহাসিক ব্যাখ্যায় বলেন, ব্যাংক বা আর্থিক প্রতিষ্ঠানে মনোনীত নমিনি গচ্ছিত অর্থের একচ্ছত্র মালিক নন। নমিনির ভূমিকা হলো, একজন ‘ট্রাস্টি’ বা ‘অছি’র মতো। এর অর্থ হলো, আমানতকারীর মৃত্যুর পর নমিনি কেবল ব্যাংক থেকে টাকা উত্তোলনের আইনগত অধিকার রাখেন। কিন্তু টাকা উত্তোলন করার পর তার দায়িত্ব হলো, উত্তোলিত অর্থ মৃত ব্যক্তির নিজ নিজ ধর্মীয় উত্তরাধিকার আইন (যেমন– মুসলিমদের জন্য ফারায়েজ আইন) অনুযায়ী প্রকৃত উত্তরাধিকারীদের মধ্যে বণ্টন করে দেওয়া। যদি নমিনি নিজেও একজন উত্তরাধিকারী হন, তবে তিনি তার প্রাপ্য অংশ পাবেন, কিন্তু সম্পূর্ণ অর্থের মালিকানা দাবি করতে পারবেন না।
এই রায়টি ছিল আইনের ব্যাখ্যায় এক অসাধারণ ভারসাম্যমূলক পদক্ষেপ, যা ব্যাংক কোম্পানি আইনকে বাতিল না করে উত্তরাধিকার আইনের সঙ্গে সমন্বয় করেছে। এর ফলে ব্যাংক নমিনিকে টাকা দিয়ে তার দায় শেষ করতে পারে, আবার উত্তরাধিকার আইনও সমুন্নত থাকে। হাইকোর্টের রায়টি যখন একটি স্পষ্ট দিকনির্দেশনা প্রদান করেছিল, ঠিক তখনই বিষয়টি আরও জটিল হয়ে ওঠে। হাইকোর্টের রায়ের বিরুদ্ধে আপিল করা হলে সুপ্রিম কোর্টের আপিল বিভাগ রায়টির কার্যকারিতার ওপর একটি স্থগিতাদেশ (stay order) জারি করেন। এর ফলে হাইকোর্টের যুগান্তকারী ‘ট্রাস্টি’ তত্ত্বটি বর্তমানে দেশের আইন (binding law) হিসেবে কার্যকর নয় এবং নমিনির আইনি অবস্থান নিয়ে এক ধরনের ধোঁয়াশা তৈরি হয়েছে।
এই আইনি শূন্যতার মধ্যে বাংলাদেশ ব্যাংক ২০১৭ সালে একটি সার্কুলার জারি করে ব্যাংকগুলোকে কঠোরভাবে ব্যাংক কোম্পানি আইনের ১০৩ ধারা অনুসরণ করার নির্দেশ দেয় এবং আমানতকারীর মৃত্যুর পর টাকা নমিনিকেই প্রদান করতে বলে। এর ফলে একটি কঠিন পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়েছে। বর্তমানে ব্যাংকগুলো নমিনিকে টাকা পরিশোধ করে দিচ্ছে এবং নমিনি সেই টাকা পেয়ে নিজেকে মালিক দাবি করে প্রায়শই প্রকৃত উত্তরাধিকারীদের, বিশেষ করে নারী ও শিশুদের তাদের ন্যায্য অধিকার থেকে বঞ্চিত করছেন।
বর্তমান পরিস্থিতিতে কোনো উত্তরাধিকারী যদি দেখেন, নমিনি টাকা দিতে অস্বীকার করছেন, তবে তাদের জন্য আদালতের দ্বারস্থ হওয়া ছাড়া উপায় নেই। প্রথমে সাকসেশন আইন ১৯২৫-এর অধীনে দেওয়ানি আদালত থেকে একটি ‘উত্তরাধিকার সনদ’ সংগ্রহ করতে হবে। এর পরও নমিনি টাকা বণ্টন না করলে উত্তরাধিকারীদের একটি ‘বাটোয়ারা মোকদ্দমা’ দায়ের করতে হয়। তবে এই পুরো প্রক্রিয়াটি অত্যন্ত সময়সাপেক্ষ, ব্যয়বহুল এবং জটিল। দুঃখজনকভাবে বর্তমান কাঠামোতে প্রকৃত অধিকারীদেরই তাদের ন্যায্য পাওনা আদায়ের জন্য সব আইনি ও আর্থিক বোঝা বহন করতে হচ্ছে।
এই অচলাবস্থা নিরসনের জন্য দুটি পথে অগ্রসর হওয়া অত্যন্ত জরুরি। প্রথমত, বাংলাদেশ সুপ্রিম কোর্টের আপিল বিভাগের উচিত দীর্ঘকাল ধরে বিচারাধীন এই মামলাটির চূড়ান্ত শুনানি করে একটি নিষ্পত্তিমূলক রায় প্রদান করা, যা দেশের সর্বোচ্চ আইন হিসেবে গণ্য হবে। দ্বিতীয়ত, একটি স্থায়ী সমাধানের জন্য সংসদ ব্যাংক কোম্পানি আইন ১৯৯১-এর ১০৩ ধারাটি সংশোধন করতে পারে। যেখানে স্পষ্টভাবে উল্লেখ করা যেতে পারে, নমিনি একজন ‘ট্রাস্টি’ হিসেবে কাজ করবেন। যতদিন পর্যন্ত এই আইনি শূন্যতা বিরাজ করবে, ততদিন হাজারো উত্তরাধিকারী, বিশেষ করে সমাজের দুর্বলতম সদস্যরা তাদের ন্যায্য অধিকার থেকে বঞ্চিত হওয়ার ঝুঁকিতে থাকবেন। তাই দেশের সর্বোচ্চ আদালত এবং আইনপ্রণেতাদের প্রতি আহ্বান– এই গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে দ্রুত পদক্ষেপ গ্রহণ করে লাখ লাখ নাগরিকের উত্তরাধিকারের অধিকার সুরক্ষিত করুন এবং আইনি ব্যবস্থায় স্বচ্ছতা ফিরিয়ে আনুন।
মো. আসাদুজ্জামান : সহকারী অধ্যাপক, আইন ডিসিপ্লিন, খুলনা বিশ্ববিদ্যালয়
asad@law.ku.ac.bd